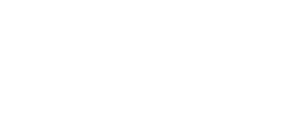বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে…………….
# ‘অত কথায় কাজ কি, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি, পৃথিবী একডাকে তাকে চেনে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী…’ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। পাণ্ডিত্য আর হৃদয়বেত্তার সঠিক আনুপাতিক মিশেলে যিনি হাস্যরসকে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, কিছুটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী, বর্ণময় এই মানুষটির জীবন পুরোপুরি রবীন্দ্ররসে জারিত ছিল। আলি সাহেব নিজেই লিখেছেন ‘এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে, আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া…’।
এই বিশিষ্ট মানুষটি শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসেবে আসেন ১৯২১ সালে। তখন মুসলিম ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে অনেক আশ্রমিকেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু জহুরির চোখ মহামূল্যবান রত্নটিকে চিনতে ভুল করেনি। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেতেই সব বাধা পেরিয়ে অবশেষে আশ্রমিকের তকমা জুটলো তাঁর। গুরুদেবের সঙ্গে মুজতবা আলির নিম্নোক্ত আলাপচারিতায় সেই সঙ্কটের আভাস কিছুটা পাওয়া যায় –
‘বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসবেন কাঁচি হাতে করে?
আমি তো অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে করে?
হাঁ হাঁ কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি দিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন আলাদা হয়ে থাকবে?’
ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এই কথোপকথনের মূল ভাবনাটি আজ প্রায় শতবর্ষ পেরিয়ে এসেও একই রকম প্রাসঙ্গিক! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আলিসাহেব তাঁর অনন্যতার নজিরটি রেখেছিলেন। গুরুদেব জানতে চাইলেন ‘কি পড়তে চাও?’ ঝটতি জবাব এসেছিল ‘তা তো ঠিক জানিনে, তবে কোনও একটা জিনিস খুব ভাল করে শিখতে চাই’। যদিও উল্টো দিক থেকে উৎসাহ পেলেন নানাকিছু শিখবার। তাঁর নিজের কথায় ‘কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম’। তার পরের ঘটনা তো ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য, আশ্রমের শিক্ষা আর বহুমুখী কর্মধারায় অবগাহন করে যেন নবজন্ম হল মুজতবার!
প্রথম প্রথম আশ্রমের অন্যরকম পরিবেশ জল, জঙ্গল, পাহাড়ের দেশ সিলেট থেকে আসা কিশোরটির ভাল লাগছিল না। একটি চিঠিতে লিখছেন ‘একে বাঙাল-খাজা বাঙাল-তদুপরি বাচাল, সর্বোপরি সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত মহিলা মিশ্রিত ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁষা তৎকালীন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আবহাওয়া বাবদে সম্পূর্ন অনভিজ্ঞ, বয়স ষোল বছর হয়-কি-না-হয়, চঞ্চল প্রকৃতির মুসলমান ছেলের পক্ষে সে বাতাবরণে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উৎকট সংকট…’। কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু সেই শান্তিনিকেতনই হয়ে উঠল তাঁর অবাধ বিচরণভূমি। আশ্রমের সমস্ত কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন সক্রিয়ভাবে। ‘বিশ্বভারতী সম্মিলনী’র নবম অধিবেশনে (১৯২২) সৈয়দ মুজতবা আলী ইদ উৎসব নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েন। সেদিনের সভার সভাপতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। মূলত, গুরুদেবের উৎসাহেই তাঁর ভাবনার স্রোত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগল। ‘শিশুমারী’ নামক প্রবন্ধে ভারতে শিশু মৃত্যুর কারণ ও তার প্রতিরোধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। প্রবন্ধ লিখেছিলেন ওমর খৈয়াম সম্পর্কেও। ভাষা শিক্ষার পাঠও চলছিল সমানতালে। রবীন্দ্রনাথের কাছে পড়েছেন ইংরেজি সাহিত্য।
একটি চিঠিতে মুজতবা আলি বলছেন ‘তিন চারদিন হইল রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ইংরাজী পদ্য পড়ানো আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন…তাঁর পদ্য পড়াইবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে – অতি নীরস পদ্যও যেন তাঁর কাছে সরস হইয়া যায়’। মুজতবার চিন্তা সর্বদা প্রথাগত পথের বাইরে গিয়ে নতুন নতুন রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করত। এই মুক্ত চিন্তার পরিসরই তো আশ্রম-শিক্ষার মূল ভাবনা ছিল! বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনো, বাকপটুতা, ‘সেন্স অব হিউমার’ তাঁকে তুমুল জনপ্রিয় করেছিল ছাত্র ও শিক্ষক মহলে। বড় ভাইয়ের পরামর্শে গান শেখাও শুরু করলেন। সেই গল্পটিও কম মজাদার নয়। স্বভাবসুলভ কৌতুক মিশিয়ে লিখছেন ‘একটি ঘণ্টা বসে কেবল সারেগামা-পাধানিসা, সানিধাপামাগারেসা সাধতে হয়। গান যে কোন দিন আরম্ভ হবে তার কোনো দিশে পাচ্ছিনে’।
১৯২৭’শে নন্দলাল বসু অঙ্কিত এবং কবিগুরু স্বাক্ষরিত ‘স্নাতক’ শংসাপত্র নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন বিদেশে। বছর দুয়েক কাবুলে কাটিয়ে গেলেন জার্মানি। পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে। ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত তাঁর কাবুল যাত্রার বিবরণ ‘দেশে বিদেশে’ পড়ে মানস ভ্রমণ করেননি এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই বইটির মাধ্যমেই সৈয়দ মুজতবা আলি বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর প্রতিটি লেখায় একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য আর রসবোধ দুয়েরই প্রতাপ ছিল প্রবল।
‘বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আমি আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব’ রবীন্দ্রনাথকে কথা দিয়েছিলেন তিনি। এসেছিলেন ফিরে ১৯৫৭ সালে। ১৯৬১-র ১৮ অগস্ট ইসলামের ইতিহাস পড়ানোর কাজে যোগ দিলেন। থাকতেন ৪৫ পল্লির কোয়ার্টারে। আশ্রমিক এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী মায়া দাসের (তিনি আলি সাহেবের ছেলে ফিরোজের পাঠভবনের সহপাঠীও বটে) মুখে শুনছিলাম, এক হাতে সাইকেল আর অন্য হাতে পোষ্য অ্যালশেসিয়ান ‘মাস্টারে’র চেন ধরে তাঁর রাজকীয় পদচারনার গল্প। মুজতবা আলি সে সময় খ্যাতির মধ্য গগনে, ফলে বিড়ম্বনাও সইতে হয়েছিল বিস্তর। কিছুটা বোহেমিয়ান জীবনে অভ্যস্ত মুজতবার বিরুদ্ধে ক্লাসে অনিয়মিত উপস্থিতি, গবেষণায় গাফিলতি ইত্যাদি অভিযোগ উঠল। উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিরোধ তখন চরমে। অকস্মাৎ ১৯৬৫’র ৩০শে জুন তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অভিমানে আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন বোলপুরের নীচুপট্টিতে, আবদুর রউফের বাড়িতে। শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসে অনেকেই ‘চাচা কাহিনি’র লেখককে দেখতে আসতেন। দরজা খুলে নিজেই বলতেন ‘আলি সাহেব তো বাড়ি নেই’। চিঠিপত্রে লিখতেন ‘শ্মশান, শান্তিনিকেতন’। খেদোক্তি করেছিলেন ‘শান্তিনিকেতনের শান্তিতো গুরুদেবর লগে লগে ঐ গেছে গিয়া…’।
১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পাকিস্থানের গুপ্তচর সন্দেহে পুলিশি হেনস্থার মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। হিন্দুধর্ম এবং ইসলামের সার বিষয়টি আত্মস্থ করেছিলেন। মহাভারত তাঁর অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। স্বভাবতই, এই অবিশ্বাস, অপমান বড় বেজেছিল হতাশাগ্রস্ত মানুষটির মনে! শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে চাননি। ভাগ্যের পরিহাসে তাঁকেই ১৯৭৪ এর ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে চিরনিদ্রায় চলে যেতে হল!
‘রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করার শক্তি আমাদের নেই’ বলেছেন ‘রবির বিশ্বরূপ’ প্রবন্ধে। লিখলেন ‘রবীন্দ্রনাথকে সে-ভাবে দেখবার মত মনীষী এখনও এ জগতে আসেননি… বড় বাসনা ছিল, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিশ্বরূপটি দেখে যাই…’ এ যেন গুরুর প্রকৃত স্বরূপ জানবার জন্য সমর্পিত এক শিষ্যের চিরকালীন আকুতি! প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রশতবর্ষে (১৯৬১) শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠান নিয়ে আক্ষেপ করে চিঠি লিখছেন ‘বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে কেউ স্মরণ করেনি। করেছে পোয়েট টেগোরকে…’।
তাঁর গুরুভক্তির উদাহরণ হিসেবে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলা যায়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রখ্যাত লেখক শংকরের সঙ্গে আলি সাহেবের দেখা হয়। সেই সাক্ষাতের বিবরণ লেখকের কলমে –
‘আমার হাত চেপে ধরে আলি সায়েব বললেন, “শংকর, মনে হচ্ছে স্মৃতি লোপ পাচ্ছে। তুমি একবার ‘সঞ্চয়িতা’খানা ধরো তো-ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখি।” ওঁর ক্লান্ত মলিন মুখে হঠাৎ হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল।’
সেদিন আবৃত্তি করেছিলেন ‘কর্ণকুন্তী সংবাদ’ একবারও না থেমে এবং নির্ভুল ভাবে। ‘সঞ্চয়িতা’র প্রতিটি কবিতার ‘পোয়েটিক ট্রান্সলেশন’ করে বিচরণ করতে চেয়েছেন কবি মানসে। ‘তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি/ গেছে সাত-ভাই চম্পা…’ এর অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজতে গিয়ে পড়ে ফেললেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবদুল জব্বারের ‘তারা-পরিচিতি’। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার এবং পুনরাবিষ্কার করে গিয়েছেন। এই হয়তো ছিল তাঁর গুরুদক্ষিণা!
কোনও এক শারদ প্রাতে, খোয়াইয়ের প্রান্তরে বসে, গুরুদেবের বাঁশিটিকে যে সু্রে বেঁধেছিলেন আলি সাহেব, তার মুর্ছনায় ভেসেছিল দেশ-বিদেশের রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে, সেই সৈয়দ মুজতবা আলিকে নিয়ে যদি বিশেষ ভাবে চর্চার একটি উদ্যোগ নেওয়া হত, তাহলে বোধহয় তাঁর ‘গুরু-মুর্শিদ’কে আমরাও নব নব রূপে আবিষ্কার করতে পারতাম!
তথ্য সূত্রঃ রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ; সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রশান্ত চক্রবর্তী, সাহিত্য একাদেমী; চরণ ছুঁয়ে যাই।, সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পিতার কর্মস্থল শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলার করিমগঞ্জে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল হবিগঞ্জের উত্তরসুর গ্রামে। তাঁর পিতা সৈয়দ সিকন্দর আলী ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। চাকরিসূত্রে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের পর মুজতবা আলী শেষপর্যন্ত শান্তিনিকেতন-এ ভর্তি হন এবং পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে ১৯২৬ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্বভারতীতে তিনি বহু ভাষা শেখার সুযোগ পান। বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ফরমিকির অধীনে তিনি সংস্কৃত ভাষা, সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন; ড. মার্ক কলিন্স ও মরিসের নিকট ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান, বগদানফের নিকট ফারসি ও আরবি এবং তুচ্চির নিকট ইতালিয়ান শেখেন। এ সময় তিনি হিন্দি ও গুজরাটি ভাষাও শেখেন। বাল্যকালে পারিবারিক সূত্রে উর্দুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।
ভারতের অন্যত্র বিশ্বভারতীর ডিগ্রি স্বীকৃত না হওয়ায় মুজতবা আলী প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা (১৯২৬) পাস করে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আই এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে ‘হুমবল্ট’ বৃত্তি নিয়ে তিনি জার্মানি গিয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি দর্শন বিভাগে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রে গবেষণা করে ১৯৩২ সালে ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৩৪-৩৫ সালে মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।
মুজতবা আলীর চাকরিজীবন শুরু হয় কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষকরূপে (১৯২৭-১৯২৯)। বরোদার মহারাজ সয়াজী রাও-এর আমন্ত্রণে ১৯৩৫ সালে তিনি বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হন। তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে খন্ডকালীন প্রভাষক হিসেবেও কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। পরে পেশার পরিবর্তন করে মুজতবা আলী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্সের সচিব ও অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মকর্তা হন। সবশেষে তিনি বিশ্বভারতীর ইসলামের ইতিহাস বিভাগে রীডার (১৯৬১) হিসেবে যোগদান করে সেখান থেকেই ১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন
শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালে হস্তলিখিত বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি সত্যপীর, রায়পিথোরা, ওমর খৈয়াম, টেকচাঁদ, প্রিয়দর্শী ইত্যাদি ছদ্মনামে আনন্দবাজার, দেশ, সত্যযুগ, শনিবারের চিঠি, বসুমতী, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখতেন। এছাড়া মোহাম্মদী, চতুরঙ্গ, মাতৃভূমি, কালান্তর, আল-ইসলাহ্ প্রভৃতি সাময়িক পত্রেরও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।
গ্রন্থাকারে তাঁর মোট ত্রিশটি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো: ভ্রমণকাহিনী দেশে-বিদেশে (১৯৪৯), জলে-ডাঙায় (১৯৬০); উপন্যাস অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শবনম (১৯৬০), শহ্র-ইয়ার (১৯৬৯); রম্যরচনা পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২) এবং ছোটগল্প চাচা-কাহিনী (১৯৫২), টুনি মেম (১৯৬৪)। মুজতবা আলীর ডি.ফিল অভিসন্দর্ভ The Origin of Khojahs and Their Religious Life Today (১৯৩৬) বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর আরেকটি অনবদ্য গ্রন্থ পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।
সৈয়দ মুজতবা আলী দেশে-বিদেশে গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রথম প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গ্রন্থখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাঠকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হন। কাবুলে অবস্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অন্তরঙ্গ উপলব্ধির ফসল এই গ্রন্থখানি। সামগ্রিকভাবে তিনি উভয় বঙ্গে সমান জনপ্রিয় ও সমাদৃত লেখক ছিলেন। আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ এই লেখকের বিশ্বমানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং অননুকরণীয় রচনাশৈলী তাঁকে এই সম্মানের অধিকারী করেছে। তদুপরি তিনি যে নৈপুণ্যের সঙ্গে বিদেশি চরিত্র ও আবহ বাংলা সাহিত্যে এনেছেন তাও তুলনাহীন। হালকা মেজাজে আড্ডার ঢঙে বলে গেলেও তাঁর অধিকাংশ রচনা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, শাস্ত্রচর্চা ও বিচার-সমালোচনায় পরিপূর্ণ।
মুজতবা আলী বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন, কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন করেছেন এবং বহুজনের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাই তাঁর লেখায় অনুরূপ বহুদর্শিতা ও নিবিড় অনুধ্যানের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর রম্যরচনাবিষয়ক ছোট ছোট রচনা পাঠকদের চিত্তবিনোদন ও অনাবিল আনন্দদানে সমর্থ হয়েছে। আবার এ কথাও ঠিক যে, তিনি হাসির আবরণে অনেক সময় হূদয়ের গভীরতর সত্যকে উদ্ঘাটন ও প্রকাশ করেছেন। তিনি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিবিধ ভাষা ও শাস্ত্র থেকে এসব উপাদান আহরণ করেন। বিশেষ করে উপন্যাস ও ছোটগল্পে মানবজীবনের অন্তহীন দুঃখ-বেদনা ও অপূর্ণতার কথা তিনি সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।
সূত্র: সংগ্রহিত।
তারিখ: মার্চ ০৫, ২০২১
রেটিং করুনঃ ,